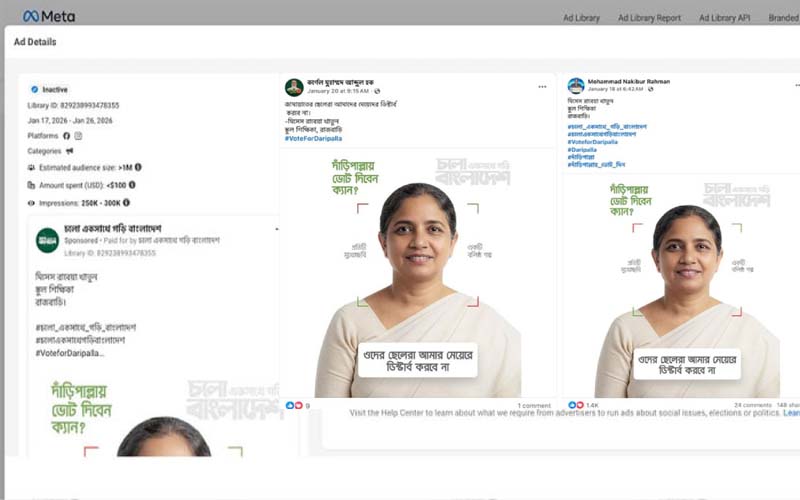“মাইট্টা গুদাম টইনর ছানি, ঝরঝরাইয়া পরের পানি। আঁই ভিজিলে যেন তেন, তুঁই ভিজিলে পরান ফাডি যায়। ও হালাচান গলার মালা পেট পুরেদ্দে তুয়ারলাই” (মাটির ঘরে টিনের ছাউনি দেওয়া, বৃষ্টি হলে ঝরঝর করে পানি গড়িয়ে পড়ে, আমি ভিজলে কোনো সমস্যা নেই তবে প্রেমিকা ভিজলে পরান ফেটে যায়।)
কথাগুলো চট্টগ্রামের জনপ্রিয় কয়েকটি আঞ্চলিক গানের। নব্বই দশকের শুরুতে কক্সবাজারের শিল্পী বুলবুল আক্তারের গাওয়া গানটি গেল বছর জনপ্রিয় শিল্পী পার্থ বড়ুয়া ও নিশিতার কণ্ঠে দেশজুড়ে আরও একবার নতুন করে জনপ্রিয়তা লাভ করে। গানের এ কলিতে মাটির ঘরের কথা তুলে ধরেন শিল্পী।
শুধু চট্টগ্রামের এ গানটি নয়, আরও বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং দেশীয় গানে রয়েছে মাটির ঘরের কথা। তবে আধুনিকতার ভিড়ে গ্রামীণ ঐতিহ্য মাটির ঘর এখন প্রায় বিলুপ্ত। গ্রামগঞ্জে এখন মাটির ঘর খুব একটা দেখা যায় না। সবাই এখন ঝুঁকছে বিল্ডিং তোলার দিকে।
জানা যায়, মাটির সহজলভ্যতা, প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রতুলতা ও শ্রমিক খরচ কম হওয়ায় আগের দিনে মাটির ঘর বানাতে আগ্রহী ছিল মানুষ। এছাড়া টিনের ঘরের তুলনায় মাটির ঘর অনেক বেশি আরামদায়ক। তীব্র শীতে ঘরের ভেতরটা থাকে বেশ উষ্ণ। আবার প্রচণ্ড গরমে থাকে তুলনামূলক শীতল।
এজন্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় মাটির ঘরের আধিক্য ছিল বেশি। এর ব্যতিক্রম ছিল না চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলাও। কিন্তু বর্তমান সময়ে মাটির ঘরের দেখা মেলাই ভার। প্রাচীনকাল থেকে মাটির ঘরের প্রচলন ছিল। এঁটেল বা আঠালো মাটি কাঁদায় পরিণত করে ২-৩ ফুট চওড়া করে দেয়াল তৈরি করা হতো। ১০-১৫ ফুট উঁচু দেয়ালে কাঠ বা বাঁশের সিলিং তৈরি করে এর ওপর খড়, টালি বা টিনের ছাউনি দেওয়া হতো।
মাটির ঘর অনেকে দোতলা পর্যন্ত করতো। এসব মাটির ঘর বানাতে কারিগরদের ৩-৪ মাস সময় লাগত। গৃহিণীরা মাটির দেয়ালে বিভিন্ন রকমের আলপনা এঁকে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তুলতেন। বন্যা বা ভূমিকম্প না হলে মাটির ঘর শতাধিক বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। মাটির ঘর নির্মাণের কারিগরদের বলা হয় দেয়ালি।
জানতে চাইলে আনোয়ারা উপজেলার রাকেশ দাশ (৭২) নামে এক দেয়ালি বলেন, মাটির ঘর তৈরি করার উপযুক্ত সময় ছিল কার্তিক মাস। কারণ এ সময় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তখন আমরা প্রতি হাত ঘর নির্মাণে ১০-১৫ টাকা করে নিতাম। আবার অনেক সময় ৫-৬ হাজার টাকা চুক্তিতেও ঘর বানিয়ে দিতাম। তবে কয়েক যুগ হলো এই পেশা ছেড়েছি। মানুষ এখন মাটির ঘর বানায় না। আবার অনেক মাটির ঘর এখন পাকা হয়ে গেছে।
রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়েনের মাটির ঘরের বাসিন্দা ইকবাল হোসেন বলেন, আমাদের মাটির ঘর আমার দাদা বানিয়েছিলেন। আমরা মাটির ঘরেই বড় হয়েছি। এখন জমি কিনে দালান করেছি, তবুও স্মৃতি হিসেবে এ মাটির ঘরটি রেখে দিয়েছি।
এ বিষয়ে বিশিষ্ট লেখক জামাল উদ্দিন বলেন, মাটির ঘর কমে যাওয়ার বিষয়টি একটি সভ্যতার চলমান ধারা। এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষ গুহায় বাস করতো। এরপর ধীরে ধীরে ঘর বানিয়ে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শুরু করে। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রভাবশালী, মাতব্বরেরা টেকসই এবং আরামদায়ক হওয়ায় মাটির ঘর তৈরি করতে শুরু করেন। মাটির ঘর-টিনের ছাউনি একটা ঐতিহ্য বহন করে।
তিনি বলেন, আধুনিকতার ছোঁয়ায় শিল্পায়নের প্রভাবে এখন বড় বড় বিল্ডিং মাটির ঘরের স্থান দখল করে নিচ্ছে। এ পরিবর্তনের ধারা শুরু হয় মূলত গ্রামের মানুষ যখন থেকে বিদেশে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে শুরু করে। জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় থেকে বাঁচার জন্য মানুষ টেকসই আবাসস্থল তৈরি করা শুরু করেছে।
তিনি আরও বলেন, ৮০ দশকের আগেও চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া, পটিয়া, আনোয়ারা, বাঁশখালী, সীতাকুন্ড, মিরসরাই, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, রাউজান, বোয়ালখালী, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ, সন্দ্বীপ ও লোহাগাড়া উপজেলায় হাজার হাজার মাটির ঘর ছিল। যা বর্তমানে পাকা দালানে পরিণত হয়েছে। তবে এসব উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায় এখনো কিছু মাটির ঘর দেখতে পাওয়া যায়। যা সংরক্ষণ করা জরুরী।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক (প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ) মো. আমিরুজ্জামান বলেন, মাটির ঘর বিলুপ্ত এখন উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে। কিন্তু এই মাটির ঘর সংরক্ষণ শুধু প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তরের একার পক্ষে সম্ভব নয়। মাটির ঘরের সাথে ভুমি বিষয়ক মালিকানা জড়িত। সেহেতু ভুমির মালিককে বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। যদি তাই হয় তাহলে প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তর সার্বিক সহযোগীতা করবে।